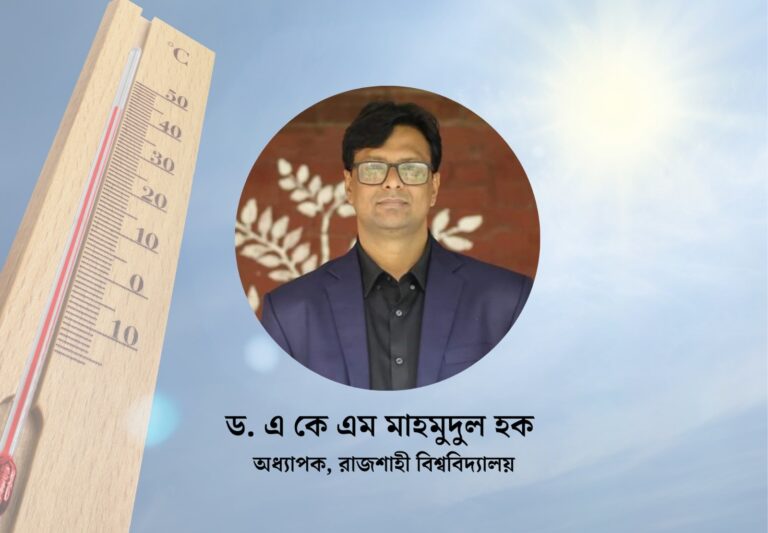বাংলাদেশে তাপমাত্রা ক্রমেই সহনীয় সীমা অতিক্রম করছে। রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরে তীব্র তাপপ্রবাহ এখন নিয়মিত দুর্যোগে পরিণত হয়েছে। ২০২৩ সালের এপ্রিল-মে মাসে টানা ৩৫ দিনের তাপপ্রবাহে শতাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে; কৃষি ও শিল্পে ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক লোকসান হয়, যা জিডিপির প্রায় ০.৪ শতাংশ।
বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, শুধু গরমজনিত কারণে প্রায় ২৫ কোটি কর্মদিবস নষ্ট হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ক্লাইমেট সেন্ট্রালের তথ্যানুযায়ী, গত জুন-আগস্ট সময়ে প্রায় ছয় কোটি মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে ঝুঁকিপূর্ণ গরমে ভুগেছে। এর ফলে দেশের ৩৪ শতাংশ মানুষ অন্তত ৩০ দিনের বেশি স্বাস্থ্যঝুঁকিপূর্ণ তাপমাত্রায় ছিল।
ঢাকার ৭৮ শতাংশ মানুষ সরাসরি এই ঝুঁকিতে রয়েছে, আর চট্টগ্রামে বছরে সর্বোচ্চ ৫৯ দিন তাপপ্রবাহ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হচ্ছে। ছয় দশকে ঢাকায় সহনীয় দিনের সংখ্যা কমেছে এবং অস্বস্তিকর গরমের দিন বেড়ে তিনগুণ হয়েছে।
উচ্চ তাপমাত্রার সাথে সাথে উচ্চ আর্দ্রতা বাংলাদেশে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। মূলত, যখন আর্দ্রতা বেশি থাকে, তখন তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম হলেও গরম অনুভূত হয়। এর কারণ হলো শরীর থেকে ঘাম বাষ্পীভূত হয়ে তাপ বের হয়ে যেতে পারে না। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় ঘাম শুকানোর প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়, ফলে শরীর ক্রমাগত গরম হতে থাকে এবং ঘাম ঝরে।
এ প্রক্রিয়া শরীরকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায়, যা ক্লান্তি ও অবসাদের জন্ম দেয়। মানুষের জন্য আরামদায়ক আর্দ্রতার মাত্রা হলো ৪০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ। এর বেশি আর্দ্রতা শুধু অস্বস্তিকর নয়, ক্ষতিকরও হতে পারে; কারণ এটি গরমের অনুভূতি বাড়ায় এবং একইসাথে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে।
বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল (মার্চ-মে) হলো বছরের সবচেয়ে উষ্ণ সময়, যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে এবং আর্দ্রতাও থাকে অনেক বেশি। এই দুইয়ের সমন্বয়ে আবহাওয়া হয়ে ওঠে অস্বস্তিকর ও ঘর্মাক্ত। গ্রীষ্মে আর্দ্রতার মাত্রা ৭০-৯০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এ সময়ে শরীর থেকে অতিরিক্ত ঘাম নির্গত হয়, যা সহজে শুকায় না।
অন্যদিকে বর্ষাকাল (জুন-সেপ্টেম্বর) প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে বাতাস প্রায় সর্বদা জলীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকে। তখন আর্দ্রতা প্রায় সবসময় ৮০-৯৯ শতাংশ এর মধ্যে থাকে, যা বছরের সবচেয়ে আর্দ্র সময়। এ সময়ে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম হলেও উচ্চ আর্দ্রতার কারণে গরমের অনুভূতি কমে না। কিন্তু বিষয়টি শুধু অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ নয়।
৯০ শতাংশের বেশি আর্দ্রতা মানবদেহের জন্য মারাত্মক হুমকি। এটি কেবল অস্বস্তিকর গরমের অনুভূতি সৃষ্টি করে না বরং সরাসরি শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর করে দেয়। সাধারণত শরীর ঘামের মাধ্যমে তাপ নির্গত করে, কিন্তু ৯০ শতাংশ আর্দ্রতায় ঘাম বাষ্পীভূত হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে শরীরের তাপমাত্রা ক্রমেই বেড়ে যায়, যা হিট স্ট্রোকের মতো জীবনঘাতী অবস্থার ঝুঁকি তৈরি করে। এ ধরনের আর্দ্রতা শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থ মানুষের জন্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক। অতিরিক্ত ঘামের কারণে শরীর থেকে দ্রুত পানি ও প্রয়োজনীয় লবণ বেরিয়ে যায়, যার ফলে পানিশূন্যতা দেখা দেয় এবং কিডনির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়। তাই এটি শুধু অস্বস্তির কারণ নয়, বরং একটি গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকির সংকেত।
গরম কতটা প্রকট বা ক্ষতিকর—তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, এর সঙ্গে কীভাবে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যায়। সুদূরপ্রসারী গরম মোকাবিলার জন্য বর্তমানে বাস্তবভিত্তিক কোনো প্রাকৃতিক সমাধান নেই। যে সমাধানকে সবাই ব্যবহার করছে কিংবা ব্যবহারের স্বপ্ন দেখছে, তা হলো এসি বা এয়ার কন্ডিশনার। এসি ঘরের তাপমাত্রা ২৫-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ধরে রাখে, যা মানুষের স্বস্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক। গবেষণা অনুযায়ী, আরামদায়ক তাপমাত্রায় কর্মীদের উৎপাদনশীলতা ৮-১১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
এছাড়া এসি বাতাস থেকে ধুলাবালি, পরাগ ও অন্যান্য অ্যালার্জেন ফিল্টার করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, এসি ব্যবহারের ফলে অ্যাজমা ও অ্যালার্জিজনিত সমস্যা প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। তাছাড়া উচ্চ আর্দ্রতাজনিত রোগ যেমন হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতেও এটি সাহায্য করে।
কিন্তু IEA-এর ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রায় ১৬০ কোটি এসি ইউনিট ব্যবহৃত হচ্ছে, যা ২০৫০ সাল নাগাদ বেড়ে ৫৬০ কোটিতে পৌঁছাতে পারে। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন বাড়িতে এসি ব্যবহার করে। অন্যদিকে ভারত, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোয় এই হার বর্তমানে ১০ শতাংশেরও কম, তবে বছরে প্রায় ১৫ শতাংশ হারে বাড়ছে।
যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোয়ও এসি ব্যবহারের প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে, তবুও বৈষম্য রয়ে যাচ্ছে মারাত্মকভাবে। এ বৈষম্য উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের কর্মদক্ষতা ও প্রবৃদ্ধিতে বড় ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে।
তাই গরমের প্রভাব যেমন বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলোয় মারাত্মক, তেমনি সমাধানের পথও অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। বাংলাদেশে গ্রীষ্মের প্রকটতা যেভাবে বাড়ছে, সর্বপ্রথম দরকার একটি আনুষ্ঠানিক হিট অ্যাকশন প্ল্যান (Heat Action Plan)। ভারতের আহমেদাবাদ বিশ্বের প্রথম শহরগুলোর মধ্যে একটি, যারা এটি প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনার আওতায় তাপপ্রবাহের আগে থেকে আগাম সতর্কতা জারি করা হয়, মানুষকে সচেতন করা হয় এবং সরকারি হাসপাতালগুলোয় অতিরিক্ত রোগীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়। এ পরিকল্পনার ফলে তাপপ্রবাহজনিত মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হয়েছে।
…এর পাশাপাশি আরেকটি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে, যাকে বলে মাইক্রোক্লাইমেটিং। আমরা জানি, তাপমাত্রা সহনীয় রাখার সবচেয়ে বাস্তবভিত্তিক উপায় হলো গাছ লাগানো। গাছ ছায়া দেয় এবং বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বাতাস ঠান্ডা করে, যা শহরের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে।
এর পাশাপাশি আরেকটি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে, যাকে বলে মাইক্রোক্লাইমেটিং। আমরা জানি, তাপমাত্রা সহনীয় রাখার সবচেয়ে বাস্তবভিত্তিক উপায় হলো গাছ লাগানো। গাছ ছায়া দেয় এবং বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বাতাস ঠান্ডা করে, যা শহরের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে।
মাইক্রোক্লাইমেট হলো একটি ছোট, সীমিত এলাকার জলবায়ু, যা আশপাশের বৃহত্তর অঞ্চলের জলবায়ু থেকে ভিন্ন থাকে। প্রতিটি বাড়ি, রাস্তা ও খোলা জায়গায় গাছ লাগানোর মাধ্যমে একটি মাইক্রোক্লাইমেট তৈরি করা সম্ভব। এটি আরবান হিট আইল্যান্ড এফেক্ট (শহরের তাপীয় দ্বীপ প্রভাব) কমাতে অত্যন্ত কার্যকর।
ঘনবসতিপূর্ণ ছোট দেশ হওয়া সত্ত্বেও সিঙ্গাপুর সফলভাবে আরবান হিট আইল্যান্ড এফেক্ট মোকাবিলা করছে। তারা ব্যাপক হারে গাছ লাগিয়ে এবং শহুরে সবুজ স্থান (Urban Green Space) বৃদ্ধি করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদের নগর পরিকল্পনায় ‘সবুজ ছাদ’ (Green Roofs) এবং ‘সবুজ দেয়াল’ (Green Walls) এখন অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে।
আরেকটি বাস্তবভিত্তিক সমাধান হতে পারে প্রতিফলক ছাদ বা কুল রুফস (Cool Roofs)। ভবনের ছাদ সাদা বা হালকা রঙের প্রতিফলক রঙে রঙ করা হলে তা সূর্যের তাপ শোষণ না করে প্রতিফলিত করে। একটি সাদা বা হালকা রঙের ছাদ সূর্যের আলো ৭০-৮০শতাংশ পর্যন্ত প্রতিফলিত করতে পারে, যেখানে একটি সাধারণ ছাদ প্রায় ৯০শতাংশ তাপ শোষণ করে।
ফলে ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যায়। এটি অত্যন্ত সাশ্রয়ী ও কার্যকর একটি পদ্ধতি, যা গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোয় ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা এবং ভারতের আহমেদাবাদের মতো উষ্ণ জলবায়ুর শহরগুলোয় কুল রুফ নীতি ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।
এছাড়া ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য ও নির্মাণশৈলীর ব্যবহার নিয়েও ভাবা যেতে পারে। বিশেষত দরিদ্র দেশগুলোয় যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এসব নির্মাণকৌশল অত্যন্ত কার্যকর। যেমন মাটির বাড়ি, খড় বা বাঁশের তৈরি ছাউনি এবং এমনভাবে বাড়ি তৈরি করা যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে।
ভারতের কিছু অঞ্চলে মাটির বাড়িগুলো শীতল রাখার জন্য ভেতরে একটি ছোট জলাধার রাখা হয় অথবা জলের উপযোগী গাছ লাগানো হয়। এ ধরনের স্থাপত্য কম খরচে প্রাকৃতিক শীতলতা নিশ্চিত করে। যদিও এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তারপরও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেখা যেতে পারে।
কাজের সময়সূচি পরিবর্তন বাংলাদেশের মতো উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ার দেশে একটি বাস্তবসম্মত ও প্রয়োগযোগ্য সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার কারণে দুপুরের দিকে শ্রমিকদের শরীর অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যায়।
যদি কাজের সময়সূচিকে দিনের শীতল অংশে স্থানান্তর করা যায়, তবে এই ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। যেমন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সকালেই পাঠদান শুরু করলে শিক্ষার্থীরা দুপুরের আগেই ছুটি পেতে পারে এবং দিনের সবচেয়ে গরম সময়ে তাদের বাইরে থাকতে হয় না। একইভাবে, প্রশাসনিক কাজ বা অফিসের কার্যক্রমও সকালে শুরু করে দুপুরের মধ্যেই শেষ করা যেতে পারে, যা একদিকে শ্রমিকদের আরামদায়ক পরিবেশ দেবে, অন্যদিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, আলো এবং ফ্যান ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সহায়ক হবে। শিল্প ও নির্মাণ খাতে এটি আরও কার্যকর হতে পারে।
বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও অতি ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তীব্র গরম মোকাবিলা করা নিছক কোনো প্রযুক্তিনির্ভর বিলাসী কাজ নয় বরং এটি টিকে থাকার লড়াই।
বাইরের পরিবেশে কাজ করতে হয় এমন শ্রমিকদের জন্য সন্ধ্যা বা রাতের শিফট কার্যকর করা হলে তারা চরম গরমের সময়ের পরিবর্তে তুলনামূলক শীতল পরিবেশে কাজ করতে পারবে, যা তাদের উৎপাদনশীলতা ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হবে। এ ধরনের সময়সূচি পরিবর্তনের ইতিবাচক দিক বিশ্বের বহু দেশে দেখা যায়।
উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় দেশগুলোয় আইনগতভাবে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বাইরের কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বাংলাদেশেও একই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।
গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে কৃষকরা ভোরে মাঠে কাজ করার অভ্যাস রপ্ত করেছেন, যা শহুরে কর্মঘণ্টার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। তাই সময়সূচি পরিবর্তন শুধু স্বাস্থ্য রক্ষা নয়, বরং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভিযোজনের জন্যও একটি কার্যকর কৌশল হয়ে উঠতে পারে।
বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও অতি ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তীব্র গরম মোকাবিলা করা নিছক কোনো প্রযুক্তিনির্ভর বিলাসী কাজ নয় বরং এটি টিকে থাকার লড়াই। এখানে উন্নত বিশ্বে ব্যবহৃত ব্যয়বহুল প্রযুক্তি বা অবকাঠামোগত সমাধান সরাসরি প্রয়োগ করা বাস্তবসম্মত নয়।
বরং কম ব্যয়সাপেক্ষ, সহজলভ্য এবং স্থানভিত্তিক অভিযোজনই হতে পারে কার্যকর উত্তরণের পথ। উদাহরণস্বরূপ, শহরে ছাদবাগান ও সবুজায়ন বৃদ্ধি, জলাশয় ও উন্মুক্ত জায়গা সংরক্ষণ, ছায়াদানকারী বৃক্ষরোপণ, পানি ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক স্বল্পব্যয়ী কর্মসূচি।
তবে এসব সমাধান কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকলে ফল পাওয়া যাবে না। প্রয়োজন নিষ্ঠার সঙ্গে ধারাবাহিক গবেষণা, যাতে জানা যায় কোন অঞ্চলে কোন পদক্ষেপ সবচেয়ে কার্যকর। পাশাপাশি দরকার সর্বোচ্চ সতর্ক পরিকল্পনা, যাতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগগুলো সমন্বিতভাবে এগিয়ে যেতে পারে। উন্নয়ন প্রকল্পে পরিবেশগত ঝুঁকি মূল্যায়ন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং শহর পরিকল্পনায় সবুজ স্থান ও জলাধারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
অতএব বলা যায়, বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রে কম খরচের, বাস্তবভিত্তিক এবং স্থানীয়কৃত অভিযোজনমূলক কৌশলই বেঁচে থাকার একমাত্র টেকসই উপায়। এই পথে সফল হতে হলে আমাদের আজ থেকেই দায়িত্বশীল নীতি প্রণয়ন, গবেষণা এবং সুপরিকল্পনার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- ড. এ কে এম মাহমুদুল হক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। সূত্র: ঢাকা পোস্ট