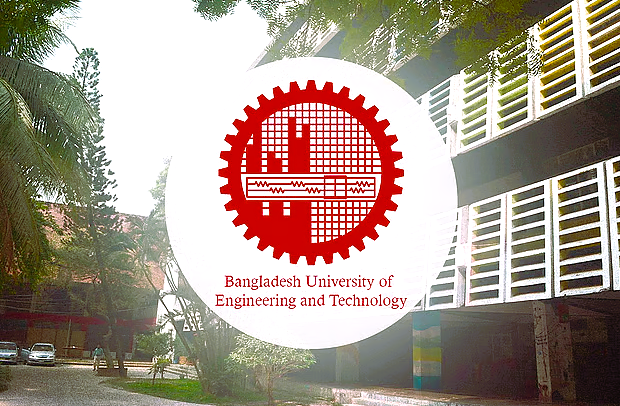কয়েক দিন আগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) গিয়েছি। বুয়েটে একটি গবেষণাকেন্দ্র আছে—রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (আরআইএসই বা রাইজ)। সেদিন রাইজের সঙ্গে দেশের ইস্পাতশিল্পের অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান জিপিএইচ ইস্পাতের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
জিপিএইচ ইস্পাতের সঙ্গে বুয়েটের সম্পর্কের কথা আমি আগে থেকেই জানতাম। বিশেষ করে তাদের কোয়ান্টাম ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস বা ৬০০ গ্রেডের ইস্পাতের সঙ্গে বুয়েটের শিক্ষক-গবেষকদের অনেক অবদান রয়েছে।
আবার দেশের কাঠামো প্রকৌশলী শিক্ষার্থীদের জন্য জিপিএইচ ইস্পাত প্রথম আলোর সঙ্গে মিলে ‘ইনজিনিয়াস’ নামে দেশজুড়ে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, সেখানেও বুয়েটের শিক্ষকেরা বিচারকের মূল ভূমিকা পালন করেন।
অনুষ্ঠানে জানলাম, এই চুক্তির অধীন বুয়েটের শিক্ষক-গবেষকেরা জিপিএইচ ইস্পাতের জন্য আলাদা করে কোনো কাজ করবেন না; বরং এই ফান্ড ব্যবহার করা হবে বুয়েটের গবেষণার ফলকে পেটেন্ট ও বাজারমুখী করার সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে।
এ জন্য দেশে-বিদেশে পেটেন্ট ফাইলিংয়ের বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন থাকবে; থাকবে বাছাই করা উদ্ভাবনগুলোকে বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ইনকিউবেশন সুবিধা। বলা বাহুল্য, কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিজের স্বার্থের পরিবর্তে সাধারণভাবে শিক্ষা-গবেষণাকে উৎসাহিত করছে—এমন উদাহরণ দেশে খুব একটা বেশি চোখে পড়ে না। তাই জিপিএইচ ইস্পাতকে সাধুবাদ জানাতে ওই অনুষ্ঠানে গিয়েছি।
শুধু চুক্তিই নয়, অনুষ্ঠানে জিপিএইচ ইস্পাতের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আরও কিছু বিষয় তুলে ধরলেন। বুয়েটের সহযোগিতায় তাঁরা যে ৬০০ গ্রেডের ইস্পাত তৈরি করেছেন, সেটি বাজারে প্রচলিত কম গ্রেডের তুলনায় একদিকে ২০ শতাংশ বেশি শক্তিশালী, অন্যদিকে সাশ্রয়ীও। ফলে একই ভবন বানাতে কম রড লাগে, খরচও কমে। বিদেশি কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীলতাও কমে।
বুয়েটের অধ্যাপক মোহর আলী ব্যাপারীর পরামর্শে তাঁরা কোয়ান্টাম ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে বিনিয়োগ করেন। এতে তাঁদের খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা। অথচ যদি তাঁরা প্রচলিত আর্ক ফার্নেস নিতেন, খরচ হতো দুই হাজার কোটির মতো। কিন্তু বাড়তি বিনিয়োগই তাঁদের আজকে আন্তর্জাতিক মানের উচ্চমানের ইস্পাত উৎপাদনে সক্ষম করেছে। দীর্ঘ মেয়াদে এ প্রযুক্তিই তাঁদের এগিয়ে রাখছে।
এমডির বক্তব্যে আরেকটি বিষয় আমাকে নাড়া দিয়েছে। তিনি বললেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখন অনেকের কাছে বোঝা মনে হলেও আসলে এটি সম্পদে রূপান্তর করা যায়। সঠিক গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে এই ১৮ থেকে ১৯ কোটি মানুষকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব।
তিনি আরো মনে করিয়ে দিলেন, গবেষণা শুধু থিসিসে আটকে থাকলে চলবে না, তার ফল বাণিজ্যিকীকরণ করতে হবে। নতুন উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ তৈরি করতে হবে। তাহলেই দেশের অর্থনীতিতে গবেষণার বাস্তব প্রভাব পড়বে।
আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গবেষণার টাকা অপ্রতুল। বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক আবু বোরহান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান সেদিন বললেন, উদ্ভাবন বা নতুন প্রযুক্তির জন্য যে বরাদ্দ আসে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। তিনি অবশ্য বলেছেন, ৫৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউজিসি চাইলেই–বা কত আর অর্থ বরাদ্দ করতে পারবে!
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এ কথাও বলেন, শক্তিশালী শিল্প মানেই শক্তিশালী গবেষণা। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যতই গবেষণা করুক, যদি শিল্পে প্রয়োগ না হয়, তবে সেই গবেষণা স্থায়ী প্রভাব ফেলে না। আবার শিল্পও যদি টেকসই না হয়, গবেষণাকে এগিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য থাকে না। শিল্প ও বিশ্ববিদ্যালয়কে তাই হতে হয় ‘দুজনে দুজনার’।
শুধু জিপিএইচ ইস্পাত নয়; আরও কিছু করপোরেট প্রতিষ্ঠানও গবেষণায় বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে। যেমন ইউনাইটেড গ্রুপ। তাদের মালিকানাধীন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ২০১৯ সালে গড়ে তোলে ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ (আইএআর)। শুরুর মূল অর্থায়ন দিয়েছে গ্রুপটি নিজেই। এর পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত ফান্ডিং করছে গবেষণায়।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও করপোরেট সহযোগিতার নজির আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দেখা যায়, পিএইচপি গ্রুপ গবেষণার একটি ফান্ডিং পার্টনার হিসেবে যুক্ত। আরো উদাহরণ হয়তো আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু এটা ঠিক যে ধীরে ধীরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার পাশে দাঁড়াতে শুরু করেছে।
কিন্তু বড় ছবিটি ভিন্ন। আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গবেষণার টাকা অপ্রতুল। বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক আবু বোরহান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান সেদিন বললেন, উদ্ভাবন বা নতুন প্রযুক্তির জন্য যে বরাদ্দ আসে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। তিনি অবশ্য বলেছেন, ৫৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউজিসি চাইলেই–বা কত আর অর্থ বরাদ্দ করতে পারবে!
এ জায়গাই আসল চিন্তার। গবেষণা মানে শুধু শিক্ষকের প্রবন্ধ বা ছাত্রের থিসিস নয়; গবেষণা মানে জাতীয় উন্নয়ন। অন্য দেশগুলো এটা বুঝেছে বলেই এগিয়েছে। ইসরায়েল গবেষণায় খরচ করে জিডিপির ৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ। দক্ষিণ কোরিয়া ৪ দশমিক ৯৬। জার্মানি ৩ দশমিক ২৯। চীন ২ দশমিক ৫৮। ভারতও শূন্য দশমিক ৭০। আর বাংলাদেশ মাত্র শূন্য দশমিক ৩০ শতাংশ। ইউরোপের অনেক দেশ, যেমন সুইডেন বা ফ্রান্স গবেষণায় ৩ শতাংশের বেশি ব্যয় করে।
সংখ্যার এই পার্থক্য আসলে উন্নয়নের পার্থক্য। যেসব দেশ গবেষণায় খরচ করেছে, তারাই নতুন প্রযুক্তি তৈরি করেছে, নতুন শিল্প গড়েছে, নতুন উদ্যোক্তা বানিয়েছে। আর যেসব দেশ তা করেনি, তারা পিছিয়ে পড়েছে।
তাহলে করণীয় কী? শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে গবেষণায় করছাড় বা ইনসেনটিভ দেওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তি স্থানান্তর সেল গড়া যায়। গবেষণার ফলাফল পেটেন্ট করতে সহায়তা দেওয়া দরকার। বাজারমুখী উদ্ভাবন বেছে নেওয়ার জন্য ইনকিউবেশন–সুবিধা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সরকারি বাজেটে গবেষণার অংশ কয়েক গুণ করা দরকার। শুধু বরাদ্দ বাড়ানো নয়, তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প ও সরকারের যৌথ পরিকল্পনায় গবেষণাকে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের মূল স্তম্ভও বানাতে হবে।
দিনের শেষে বিষয় একটিই—শিল্প আর বিশ্ববিদ্যালয় যদি হাতে হাত মেলায়, তবেই বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের পথে এগোতে পারবে।
-
মুনির হাসান; প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও যুব কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক।