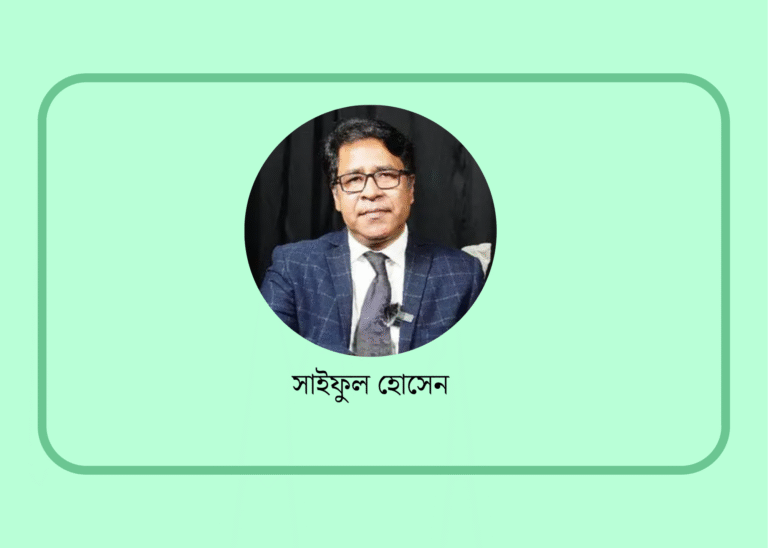অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদকালে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি। এর মূল কৌশল হলো সুদের হার বাড়ানো, যাতে বাজারে টাকার প্রবাহ কমানো যায়। নীতি অনুযায়ী মানুষ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সহজে ঋণ নিতে পারবে না। ফলে বাজারে অর্থের চাহিদা কমে যায় এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে থাকে।
বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৩ সালের মে থেকে ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১১ বার রেপো রেট বাড়িয়েছে। ২০২৩ সালের শুরুতে নীতিগত সুদের হার ছিল ৫ শতাংশের নিচে। এক বছরেরও কিছু বেশি সময়ে তা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময় ব্যাংকগুলো ধারাবাহিকভাবে সুদের হার বাড়িয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে নতুন ঋণ গ্রহণ ও বিনিয়োগে। বাজারে নতুন ঋণ ও বিনিয়োগে একটি ধরনের স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক ধারাবাহিকভাবে নীতিগত পরিবর্তন বাস্তবায়ন করে ইঙ্গিত দিচ্ছে, তাদের প্রধান লক্ষ্য মুদ্রাস্ফীতি এক অঙ্কে নামানো। অর্থাৎ টাকার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো এবং দাম স্থিতিশীল রাখা। তবে এসব প্রয়াস সত্ত্বেও প্রত্যাশিত ফল এখনও দেখা যায়নি। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে দেশের সাধারণ মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ১১.৬৬ শতাংশে, যা বিগত এক দশকের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। অর্থাৎ নীতিগত সুদের হার বাড়ালেও বাজারে দ্রব্যমূল্যের চাপ তেমন হ্রাস পাচ্ছে না।
অর্থনীতিবিদদের মতে, সুদের হার বাড়ানোর মতো ‘একমুখী পদক্ষেপ’ হয়তো কিছু সময়ের জন্য চাহিদা কমাতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি কেবল চাহিদা-চলিত নয়; সরবরাহ-চলিতও। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও খাদ্যের দাম বৃদ্ধি, টাকার অবমূল্যায়ন এবং আমদানিনির্ভর পণ্যের খরচ বেড়ে যাওয়ায় সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে বাজারে পণ্যের সংকট তৈরি হচ্ছে, যা শুধু সুদের হার বাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব।
এই বাস্তবতায় সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রয়োগ সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। বরং ব্যবসা-বাণিজ্যে ঋণপ্রবাহ হ্রাস পেয়েছে, বিনিয়োগ কমেছে এবং উৎপাদন খরচ বেড়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে দেশের ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ছিল ১১.৬৬ শতাংশ, যা এখনও বেশি।
প্রকৃতপক্ষে, শুধু মুদ্রানীতি কঠোর করলেই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। বাজারের বিকৃতি, সরবরাহ চেইনের সমস্যা এবং টাকার অবমূল্যায়নও এখানে বড় ভূমিকা রাখে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রান্নাঘরে চুলা আছে, কিন্তু গ্যাস আসে না। রান্নার উপকরণের দাম বেড়ে গেছে, আগুন ঠিকমতো জ্বলে না। তখন রান্না দেরিতে হবে আর খাবারের দাম বাড়বে। শুধু গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমালে সমস্যা মিটবে না; পুরো রান্নার ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে।
ঠিক তেমনি, বাংলাদেশে শুধু সুদের হার বাড়ানোই যথেষ্ট নয়। সমস্যার মূল বিষয়টি লুকিয়ে আছে অর্থনীতির কাঠামোগত দুর্বলতায়। যেমন উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, আমদানিনির্ভরতা এবং সরবরাহ ব্যবস্থার জটিলতা।
অর্থনীতিবিদরা কিছু সহজ ভাষার সুপারিশ দেন। প্রথমত, মুদ্রানীতির সঙ্গে ফিসক্যাল নীতিকে একসঙ্গে কার্যকর করতে হবে। অর্থাৎ বাজেট ঘাটতি কমানো, কর সংগ্রহ বাড়ানো এবং সরকারি ব্যয় কার্যকর করা। দ্বিতীয়ত, সরবরাহ চেইন ও উৎপাদন খাত মজবুত করতে হবে। কৃষিতে ইনপুট খরচ কমানো, শিল্পে স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার বাড়ানো এবং আমদানির খরচ কমানো জরুরি। তৃতীয়ত, বাজারে প্রতিযোগিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। সিন্ডিকেট ও মধ্যস্বত্বভোগীর দখল কমানো দরকার। চতুর্থত, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।
পরিশেষে বলা যায়, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সংকোচনমূলক নীতি বেশ কয়েকবার নিয়েছে। কিন্তু সুদের হার বাড়িয়েও মুদ্রাস্ফীতি দ্রুত কমছে না। পাশাপাশি উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অর্থাৎ শুধু সুদের হার বাড়ানো যথেষ্ট নয়। বরং সেই নীতির সঙ্গে অন্যান্য সংস্কার ও নীতি একসঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে। না হলে মুদ্রাস্ফীতি কমবে ধীরে এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি বাড়বে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়ন চেইন সক্রিয় রাখতে হলে ‘মুদ্রানীতি + ফিসক্যাল নীতি + সরবরাহ চেইন সংস্কার + বিনিয়োগ পরিবেশ’ এই চারটি একসঙ্গে গুরুত্ব পাবে।
সূত্র: সাইফুল হোসেন: ব্যাংকার ও আর্থিকবিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও কৌশল বিশেষজ্ঞ।