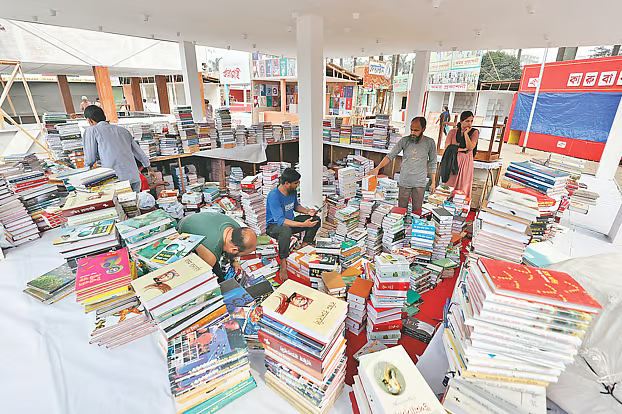পরীক্ষাটা ছিল খুবই সহজ; আর কাজটাও হয়তো অনেকের কাছে সহজই মনে হতে পারে।আমেরিকার দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের হাতে দেওয়া হলো চার্লস ডিকেন্সের বিখ্যাত উপন্যাস ‘ব্লিক হাউস’-এর প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদ। তাদের বলা হলো, মন দিয়ে পড়ে এর অর্থ বুঝিয়ে দিতে। সোজা কথায়, ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদেরকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের একটু ইংরেজি সাহিত্য পড়তে দেওয়া হয়েছিল। কাজটা আর কতটা কঠিন হতে পারে?দ
কিন্তু দেখা গেল, কঠিন তো বটেই, কাজটা প্রায় অসম্ভব। আইনি ভাষার মারপ্যাঁচে ছাত্রছাত্রীরা একেবারে হতবুদ্ধি। রূপকের ঘনঘটায় তারা খেই হারিয়ে ফেলল। ডিকেন্সের কুয়াশার যে বর্ণনা, তা পড়ে তারা নিজেরাই যেন ঘোর কুয়াশায় পথ হারাল। সাধারণ শব্দভান্ডারের অবস্থাও তথৈবচ: এক ছাত্র তো ‘হুইস্কার্স’ শব্দটার মানে ভেবে বসেছিল, বোধহয় কোন জন্তুর নাম। সমস্যাটা শুধু সাহিত্যবোধের অভাব নয়, বরং তাদের অক্ষরজ্ঞানটাই যেন তলানিতে এসে ঠেকেছে।
পড়ার অভ্যাসটাই যেন আজ সংকটের মুখে। দেশে দেশে বিভিন্ন গবেষণায় একই চিত্র বারবার ফুটে উঠছে। প্রাপ্তবয়স্করা কম পড়ছে। শিশুরা কম পড়ছে। কিশোর-কিশোরীদের পড়ার পরিমাণ তো আশঙ্কাজনকভাবে কম। ছোট শিশুদের বই পড়ে শোনানোর চলও কমে আসছে; অনেককে তো শোনানোই হয় না।
দরিদ্র পরিবারের শিশুদের মধ্যে পড়ার হার কম—এই ঘটনাকে ‘রিডিং গ্যাপ’ বলা হয়। কিন্তু আসল সত্যিটা হলো, পড়ার অভ্যাস কমছে সবার, সর্বত্র। আমেরিকায়, গত ২০ বছরে আনন্দের জন্য বই পড়া মানুষের সংখ্যা দুই-পঞ্চমাংশ কমে গেছে, এই তথ্য উঠে এসেছে ‘আইসায়েন্স’ নামক এক জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায়। পোলিং সংস্থা ইউগভ দেখেছে যে, ২০২৪ সালে ৪০ শতাংশ ব্রিটিশ কোনো বই পড়েননি বা শোনেননি। আর শুধু আনন্দের পড়া কেন, অপছন্দের পড়ার অবস্থাও তথৈবচ। যেমনটা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইংরেজির অধ্যাপক স্যার জোনাথন বেটস বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের ‘তিন সপ্তাহে একটা উপন্যাস শেষ করতেও নাভিশ্বাস ওঠে।’
আরেকজন বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী তো বলেই ফেলেছিলেন, এখনকার শিক্ষিত তরুণদের মধ্যেও ‘মনোযোগ দিয়ে কোনো কাজ করার অভ্যাসটা নেই।’
অবশ্য এই ধরনের আক্ষেপকে একটু সন্দেহের চোখে দেখা উচিত।
বইপ্রেমীরা বইয়ের চেয়েও বেশি যা ভালোবাসেন, তা হলো বইপড়ার অভ্যাস নিয়ে অভিযোগ করা। তারা চিরকালই এটা করে এসেছেন। উপরে উল্লেখিত সেই ‘বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী’ আর কেউ নন, স্বয়ং ডিকেন্স, এবং পরিহাসের বিষয় হলো, কথাটা তিনি লিখেছিলেন তাঁর ‘ব্লিক হাউস’ উপন্যাসে।
একটা সময় ছিল যখন মানুষ লেখা বা পড়ার বিস্তারকে সন্দেহের চোখে দেখত। অনেকে আশঙ্কা করতেন যে, লেখার ওপর নির্ভরশীলতা মানুষের স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেবে। মানুষ আর কিছু মনে রাখার চেষ্টা করবে না, কারণ সবকিছু তো লেখাই থাকবে। সেই পুরোনো ভয়গুলো যখন কেটে গেল, অর্থাৎ মানুষ যখন পড়ালেখা এবং বইকে জীবনের অংশ হিসেবে মেনে নিল, ঠিক তখনই শুরু হলো নতুন ভয়—এই পড়ার অভ্যাসটা না আবার হারিয়ে যায়!
তবে তর্কসাপেক্ষে বলা যায়, এখন যা ঘটছে, তা সত্যিই নতুন। মানুষ কেবল কম পড়ছে তাই নয়; যা পড়ছে, তার ধরণটাও বদলে যাচ্ছে। বাক্য ছোট ও সরল হয়ে আসছে। নিউইয়র্ক টাইমসের কয়েকশ বেস্টসেলার বই বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৩০-এর দশকের তুলনায় জনপ্রিয় বইয়ের বাক্য প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছোট হয়ে গেছে।

ভিক্টোরিয়ান যুগের বেস্টসেলার জন রাসকিনের লেখা ‘মডার্ন পেইন্টার্স’ এর প্রথম বাক্যটিই ১৫৩ শব্দের। সেখানে কড়া ভাষায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের ‘ভ্রান্ত মতামতকে’ বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং একটি উপশিরোনামে লেখা: ‘জনমত শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়।’ অন্যদিকে, আমাজনের বর্তমান নন-ফিকশন বেস্টসেলার মেল রবিন্সের লেখা ‘দ্য লেট দেম থিওরি’ বইয়ের প্রথম বাক্যটি মাত্র ১৯ শব্দের। এর একটি উপশিরোনাম হলো ‘আমি যেভাবে আমার জীবন বদলেছি।’
পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়ার জন্য দোষারোপ করা হয় স্মার্টফোনকে—এবং এটা সত্যি যে মনোযোগ সরানোর মতো জিনিসের সংখ্যা এখন অনেক বেড়েছে। কিন্তু বই পড়া বরাবরই একটা ঝামেলার কাজ। প্রাচীন গ্রিক কবি ক্যালিমাকাস বলেছিলেন, ‘বড় বই এক বড় উপদ্রব।’ বিশেষ করে দুপুরবেলা খাওয়ার পর এই কথাটি আরও বেশি সত্যি। আপনি পড়তে বসলেন, আর তখনই, যেমনটা একজন লেখক লিখেছিলেন, জানলা দিয়ে রোদ এসে ঘরে ঢোকে, দিনটাকে ‘৫০ ঘণ্টা লম্বা’ মনে হয়, পাঠক ‘চোখ রগড়াতে থাকেন’ এবং শেষে বইটা ‘মাথার নিচে দিয়ে…হালকা ঘুমে তলিয়ে যান।’ সেই পাঠক যেহেতু চতুর্থ শতাব্দীর একজন সন্ন্যাসী ও তপস্বী ছিলেন, তাই তিনি সম্ভবত স্ন্যাপচ্যাটের মতো কিছুর দ্বারা বিভ্রান্ত হননি।
সুতরাং, ব্যাপারটা কেবল মনোযোগ সরানোর উপকরণের নয়, পড়ার প্রতি সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষাটাই যেন কমে গেছে। ভিক্টোরিয়ান যুগে আত্ম-উন্নয়নের জন্য নানা সমিতি গড়ে উঠেছিল। জনাথন রোজ তাঁর অনবদ্য বই ‘দ্য ইন্টেলেকচুয়াল লাইফ অফ দ্য ব্রিটিশ ওয়ার্কিং ক্লাসেস’-এ লিখেছেন, স্কটল্যান্ডের পাহাড়ে মেষপালকরা ‘এক ধরনের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি’ চালাত। প্রত্যেক মেষপালক দেয়ালের ফোকরে অন্য মেষপালকদের পড়ার জন্য বই রেখে যেত। ভিক্টোরিয়ান যুগের কারখানা-শহরগুলোতে শ্রমিকরা টাকা জমিয়ে বই কিনত। স্কটল্যান্ডের এক জায়গায় এক বালক এক ফেরিওয়ালাকে বই পড়তে দেখেছিল। সেই বইটি—যা ফেরিওয়ালা তাকে ধার দিয়েছিল—ছিল থুসিডাইডিসের লেখা। আর সেই বালকটি ছিলেন র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড, যিনি পরে ব্রিটেনের প্রথম লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।
আজ আত্ম-উন্নয়নের সেই উদ্যম কমে গেছে। কেউ কেউ বইয়ের চড়া দাম আর লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাওয়াকে আজকের এই বৌদ্ধিক উদাসীনতার জন্য দায়ী করেন—কিন্তু বইয়ের দাম এখনকার চেয়ে সস্তা আগে কখনও ছিল না। রোমান যুগে একটা বইয়ের দাম ছিল প্রায় একটা উটের তিন-চতুর্থাংশ (অর্থাৎ অনেক)। ভিক্টোরিয়ান যুগে লর্ড বায়রনের ‘চাইল্ড হ্যারল্ড’স পিলগ্রিমেজ’ বইয়ের একটা কপির দাম ছিল একজন শ্রমিকের প্রায় আধ সপ্তাহের রোজগারের সমান। আর তবুও, আঠারো শতকের শেষে স্কটল্যান্ডের স্বশিক্ষিতদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ। আজ ‘চাইল্ড হ্যারল্ড’স পিলগ্রিমেজ’ কিন্ডলে বিনামূল্যে পাওয়া যায়, আর পাঠকরা এক কাপ কফির থেকেও কম দামে অনেক বই খুঁজে নিতে পারেন। কিন্তু পড়ার হার কমেই চলেছে।
এর একটা সোজাসাপ্টা ব্যাখ্যা হলো, মানুষের আর এসব করতে ইচ্ছে করে না। অধ্যাপক বেটস ছাত্রছাত্রীদের না পড়া নিয়ে মন্তব্য করে অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তিনি নিজেও স্বীকার করেন যে, এই ধরনের কথা বললে তাঁকে সেকেলে মনে হতে পারে। কিন্তু অধ্যাপকদের সাথে কথা বললেই বোঝা যায়, ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যাওয়া নিয়ে তারা সবাই হতাশ। অধ্যাপক রোজ যখন পড়ানো শুরু করেছিলেন, তখন তিনি ‘ব্লিক হাউস’ পড়াতেন। তিনি বলেন, আজ আর সেটা পড়ানোর চেষ্টা করবেন না, কারণ একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ‘আরও কম পড়ার’ জন্য ‘ক্রমাগত চাপ’ থাকে, তেমনই ‘ছাত্রছাত্রীরা কিছুতেই দীর্ঘ লেখা পড়বে না।’ একাধিক সমীক্ষায় তরুণ-তরুণীরা বই পড়াকে ‘বিরক্তিকর’ এবং ‘বাধ্যতামূলক কাজ’ বলে বর্ণনা করেছে।
বই না পড়লে কী ক্ষতি?
অনেকে বলবেন, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরা সাক্ষরতা কমে যাওয়া নিয়ে দুঃখ করতেই পারেন, কিন্তু সেটা তো তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণেও হতে পারে। পড়ার অভ্যাস কমার থেকে বেশি তাদের চিন্তা হয়তো ছাত্রছাত্রী কমে যাওয়া নিয়ে। কিন্তু সাক্ষরতার প্রভাব শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার তালিকার ওপর পড়ে না। একটি উদাহরণ হলো, সাহিত্যের জ্ঞান বাড়লে রাজনৈতিক জ্ঞানও বাড়ে। সহজভাবে বললে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এথেন্সের মানুষরা ‘অস্ট্রাসিজম’ চর্চা শুরু করতে পেরেছিল—অর্থাৎ, পাত্রের ভাঙা টুকরোর ওপর নাম লিখে কাউকে নির্বাসনে পাঠানোর জন্য ভোট দেওয়া। শিক্ষাবিদ উইলিয়াম হ্যারিস যেমনটা দেখিয়েছেন, এর কারণ হলো তারা ‘একটা নির্দিষ্ট মাত্রার সাক্ষরতা’ অর্জন করেছিল।
বিপরীতভাবে, সাহিত্যের জ্ঞান কমলে রাজনৈতিক জ্ঞানও কমতে পারে। ব্রিটেনের সংসদীয় ভাষণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত এক দশকে ভাষণের আকার এক-তৃতীয়াংশ কমেছে।
২৫০ বছরের মার্কিন রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণকে ফ্লেশ-কিনকেড রিডেবিলিটি টেস্ট বা পাঠযোগ্যতার একটি পরীক্ষা ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় জর্জ ওয়াশিংটনের ভাষণের স্কোর ছিল ২৮.৭, যা স্নাতকোত্তর স্তরের। আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষণের স্কোর ছিল ৯.৪, যা একজন হাইস্কুলের ছাত্রের পড়ার স্তরের সমান।
এটা যে সবদিক থেকে খারাপ, তা নয়। অনেক সময় সহজ গদ্যই ভালো গদ্য, আর রাজনীতিবিদদের ভাষণ আরও লম্বা হোক, এমনটা খুব কম মানুষই চায়। কিন্তু অধ্যাপক বেটসের ভাবনা আরও গভীর। তিনি আশঙ্কা করেন, জটিল গদ্য পড়ার ক্ষমতা হারালে, মানুষ হয়তো জটিল ধারণা তৈরি করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলবেন, যা ‘সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝতে এবং দুটো পরস্পরবিরোধী চিন্তাকে একসাথে ধরে রাখতে সাহায্য করে।’
পড়ার অভ্যাস কমে গেলে আরও অনেক ক্ষতি হবে। সামাজিক উন্নতির জন্য পড়ার চেয়ে কার্যকর উপায় খুব কমই আছে—স্কটল্যান্ডের সেই মেষপালকেরাই যার উদাহরণ। ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা হয়তো বেশি পড়ে, কিন্তু পড়া এমন এক আবিষ্কার যা ধনী-গরিব মানে না। গৃহশিক্ষক, বন্ধু বা নামীদামী স্কুল—কেউই কাউকে বই পড়তে বাধ্য করতে পারে না, যতক্ষণ না কেউ নিজে চাইছে। পড়া শুধু একটা উপায় নয়, এটা জীবনের অন্যতম বড় আনন্দও, যেমনটা ডিকেন্স ভালোভাবেই জানতেন। ‘গ্রেট এক্সপেকটেশনস’ উপন্যাসের দয়ালু কামার জো যেমনটা বলেছিল: ‘আমাকে একটা ভালো বই দাও…আর একটা গনগনে আগুনের সামনে বসিয়ে দাও, এর চেয়ে ভালো আর কিছু আমি চাই না।’ মানুষ যেদিন এই আনন্দটা ভুলে যাবে, সেদিনটা সত্যিই বড় অন্ধকার মনে হবে।