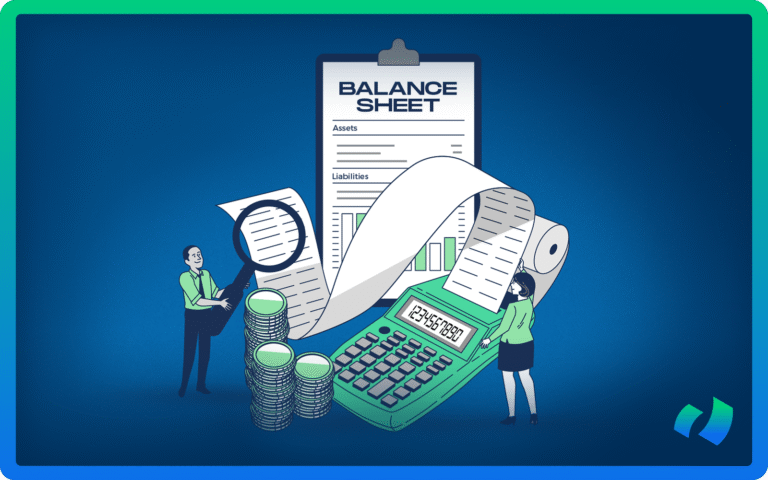বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত বর্তমানে শক্তিশালী আর্থিক চিত্রের আড়ালে ভারসাম্যহীনতা ও গভীর ঝুঁকিতে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাংকগুলোর ব্যালান্সশিটে শীতলভাবে দেখানো আয়-ব্যয় ও সম্পদ-দায়ের হিসাব পাঠকের কাছে সহজেই আকর্ষণ করে, কিন্তু গোলাকার সংখ্যা ও নিখুঁত উপস্থাপনার পিছনে লুকিয়ে আছে নিম্নমানের সম্পদ (non-performing loans – NPL), বৃহৎ পরিসরের খেলাপি ঋণ, ক্যাপিটাল সংকট এবং ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। ২০২৪ সালের শেষদিক থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে মোট NPL হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে; একইসঙ্গে খাতে বৃহৎ ক্যাপিটাল ঘাটতি ও একাধিক বড় ধারকের বিরুদ্ধে মামলার উদ্বেগ ব্যাংকিং সিস্টেমের স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে।
“ব্যালান্স শিটে হাসি, বাস্তবে কান্না” এই শিরোনামটি কেবল কাব্যিক নয়; এটা ব্যাংকের আর্থিক বিবরণের দুই-চিত্রকে নির্দেশ করে। একদিকে ব্যাংকের বিবরণীতে তরলতা, আয়, সম্পদ বৃদ্ধি, সবকিছু ‘হাস্যোজ্জ্বল’; অন্যদিকে মাঠপর্যায়ে আমানতকারীর অনিশ্চয়তা, ঋণের মানহ্রাস, বড়ো খেলাপিদের ঋণ উদ্ধার না করা এবং সমস্যার চরম প্রকোপ- ‘বাস্তবে কান্না’। এই দ্বৈততা অনুধাবন না হলে পাঠক-কল্যাণ ও নীতি-প্রতিষ্ঠানের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হবে। আলোচ্য প্রতিবেদনে আমরা এই দ্বৈততার মূল কারণ ও ফলাফল খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালিয়ে যাবো।
বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে এখন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের যুগ চলছে। কাগজে-কলমে অর্থাৎ ব্যালান্স শিটে দেখা যায় সবকিছু ঠিকঠাক, আমানতের পরিমাণ বেড়েছে, ঋণ বিতরণও মোটামুটি ভালো, আর খেলাপি ঋণের হার নিয়ন্ত্রণে, এমন এক ছবি আঁকা হয়। কিন্তু মাঠের বাস্তবতা একেবারেই উল্টো। গ্রাহক টাকা তুলতে গেলে ব্যাংকে “ক্যাশ নেই”, ব্যবসায়ীরা নতুন ঋণ পেতে হিমশিম খাচ্ছে, আর আস্থার সংকটে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। ব্যালান্স শিটের হাসির আড়ালে তাই আজ ব্যাংক খাতের এক গভীর কান্না লুকিয়ে আছে।
ব্যাংকের ব্যালান্সশিটে মূলতঃ দুইটি বড় অংশ থাকে: সম্পদ (Assets) এবং দায় (Liabilities)। ব্যাংকের প্রধান সম্পদ হলো ঋণ (Loans) ও বিনিয়োগ; প্রধান দায় হলো আমানত। ব্যাংক যে সমস্যায় পড়ে তা সাধারণত সম্পদ-পক্ষের মানহ্রাস যেমন: NPL বৃদ্ধি বা দায়-পক্ষের অপ্রতুলতা যেমন: আমানত প্রত্যাহার বা তীব্র সংক্ষিপ্ততা। NPL বেড়ে গেলে ব্যাংকের লাভ-ক্ষতি হঠাৎ বদলে যেতে পারে; আর ক্যাপিটাল সংকট হলে সেটি ব্যাংককে পুনঃপুঁজি করতে বাধ্য করে নীতিনির্ধারক বা সরকারিক উৎসের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। এই রিপোর্টে আমরা ব্যাংকের ‘ব্যালান্সশিটে হাসি’ বলতে বোঝাবো কীভাবে রিপোর্টগুলোতে সাময়িক সুদ/অস্থায়ী মুনাফা দেখানো হয়, আর ‘বাস্তবে কান্না’ বলতে বোঝাবো কীভাবে আভ্যন্তরীণ প্রবাহ-রীতি, খেলাপি ঋণ এবং অদক্ষ পরিচালনা সিস্টেমে ঝুঁকি তৈরি করে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, গত জুলাই শেষে ব্যাংক খাতে আমানতের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৮ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। আগস্ট শেষে সেটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯ লাখ ৪ হাজার ৭৪০ কোটি টাকায়। অর্থাৎ মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে (জুলাই-আগস্ট) ব্যাংক খাতে আমানত বেড়েছে ২৪ হাজার ৬৩২ কোটি টাকা। শুনতে আশাব্যঞ্জক, কিন্তু বাস্তবে এর বড় অংশই “অলিখিত সংকটে” বন্দি।কারণ এই অর্থের বড় অংশই সরকারি সঞ্চয়, প্রবাসী আয় এবং করপোরেট আমানত, যেগুলোর ব্যবহারিক প্রবাহ সীমিত। অন্যদিকে ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণে দেখা যাচ্ছে কাগজে চমকপ্রদ বৃদ্ধি ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত প্রায় ১৫ দশমিক ৪ লাখ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের হিসাব দেখানো হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কার্যকরভাবে ফেরতযোগ্য ঋণের হার ক্রমেই কমছে। অর্থাৎ টাকা যাচ্ছে, কিন্তু ফিরছে না; অথচ ব্যালান্স শিটে সব ঠিকঠাক।
এদিকে টানা ১৭ মাস পর ব্যাংক আমানতের প্রবৃদ্ধি দুই অঙ্কের ঘরে ফিরেছে। চলতি বছরের আগস্ট মাস শেষে আমানতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক শূন্য ২ শতাংশে। এর আগে সর্বশেষ ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমানতের প্রবৃদ্ধি ছিল ১০ দশমিক ৪৩ শতাংশ। চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রবৃদ্ধি নেমে গিয়েছিল ৮ দশমিক ৫০ শতাংশে। ২০২৪ সালের মার্চ থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত সময়জুড়ে ব্যাংক আমানতের প্রবৃদ্ধি ছিল এক অঙ্কে। এই ভুয়া সাফল্যের গল্প তৈরির কৌশলও আজ অনেক ব্যাংক আয়ত্ত করেছে। ঋণ পুনঃতফসিল, রিশিডিউলিং, রাইট অফ, এই সব হিসাবি পদক্ষেপে খারাপ ঋণকে কাগজে ভালো বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকের লাভ নাকি বেড়েছে, অথচ সেই লাভের পেছনে নগদ প্রবাহ নেই।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ (২০২৫) প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৪ সালের জুনে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ২০২৫ সালের জুন শেষে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার ৪২৮ কোটি টাকায়, অর্থাৎ এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় ৩ লাখ ১৯ হাজার ৩৭ কোটি টাকা। বর্তমানে এটি বিতরণ করা মোট ঋণের ২৭ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ, অর্থাৎ ব্যাংক খাতের মোট ঋণের প্রায় চার ভাগের এক ভাগেরও বেশি ইতিমধ্যে খেলাপি হয়ে গেছে।
অপরদিকে ২০২৫ সালের মার্চ শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৪ লাখ ২০ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা, যা ছিল বিতরণ করা ঋণের ২৪ দশমিক ১৩ শতাংশ। কিন্তু জুন ২০২৫ (সেপ্টেম্বর শেষে প্রকাশিত) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৬৭ হাজার কোটি টাকা, যা মোট বিতরণ করা ঋণের প্রায় ৩৩ শতাংশ। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমবারের মতো জানিয়েছে যে, দেশে বর্তমানে ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপির সংখ্যা ৩ হাজার ৪৮৩ জন।
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর অবস্থাই সবচেয়ে বেশি নাজুক। সংশ্লিষ্ট ছয়টি ব্যাংক সোনালী, অগ্রণী, জনতা, রূপালী, বেসিক ও বিডিবিএল; এই ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণের বোঝায় ন্যুব্জ। অন্যদিকে বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলো আবার পারিবারিক মালিকানা, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রভাবের শিকার। ব্যাংকের লাভের ঘোষণা, ডিভিডেন্ড বণ্টন বা রিজার্ভ হিসাব সবকিছুতেই এক ধরণের সাজানো বাস্তবতা। একজন অর্থনীতিবিদের ভাষায়, “আমাদের ব্যাংকগুলো এখন মেকআপ করা মডেলের মতো; বাইরে ঝলমলে, ভিতরে ক্লান্ত।”
২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ উত্তোলনের প্রবণতা বেড়েছে ২৪%, যা একটি রেকর্ড। গ্রাহকরা এখন ব্যাংকে টাকা রাখতেও ভয় পাচ্ছে, তুলতেও ভয় পাচ্ছে।বহু ব্যাংকে দেখা গেছে বড় অঙ্কের চেক নিলেও ক্যাশে টাকা নেই, গ্রাহককে বলা হয় “পরের সপ্তাহে আসেন”। এই অবস্থাকে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, “লিকুইডিটি প্যারালাইসিস” অর্থাৎ তারল্য আছে কাগজে, কিন্তু হাতে নগদ নেই। বেশ কিছু ছোট ও মাঝারি ব্যাংক এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিফাইন্যান্স স্কিমে টিকে আছে। অর্থাৎ তারা নিজেদের অর্থ দিয়ে কাজ চালাতে পারছে না; কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তায় দিন গুজরান করছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি বিভাগ (BRPD) থেকে শুরু করে ব্যাংক বোর্ড পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই অদক্ষতা ও প্রভাবের ছায়া। যেখানে বিশ্বমানের ব্যাংকগুলোতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) ও ক্রেডিট অ্যানালাইসিস কঠোরভাবে পরিচালিত হয়, সেখানে আমাদের অনেক ব্যাংক এখনও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে ঋণ অনুমোদন দেয়। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ৭০% বড় খেলাপি ঋণই রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে। তারা ঋণ নেয়, পরিশোধ করে না, পরে আবার “নতুন তফসিল” পায়। ফলে সৎ ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই চক্রটি ব্যাংকিং ব্যবস্থার শিরা-উপশিরায় বিষের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।
২০২৫ সালের অক্টোবর নাগাদ দেশে মুদ্রাস্ফীতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯ দশমিক ৪%। অন্যদিকে ব্যাংকে গড় আমানত সুদের হার মাত্র ৫ দশমিক ৮%। অর্থাৎ আমানত রাখলে আসলে মানুষ ক্ষতিই করছে, প্রকৃত অর্থে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা উচ্চ সুদে ঋণ নিচ্ছে ১১-১২% হারে। ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মূল ভূমিকা অর্থ প্রবাহের ভারসাম্য রক্ষা, সেটাই বিঘ্নিত হচ্ছে।একে বলা যায়, “অসামঞ্জস্যের অর্থনীতি”।
বাংলাদেশ ব্যাংক একদিকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়, অন্যদিকে ব্যাংকগুলোর তারল্য সংকট নিরসনে আবার রিফাইন্যান্স স্কিম চালু করে। ফলে নীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, “নীতিগত অনিশ্চয়তা ব্যাংক খাতের সবচেয়ে বড় সংকট। যে নীতিতে আজ সিদ্ধান্ত হয়, কাল সেটি বদলে যায়।” এই নীতিগত দোলাচল ব্যাংকগুলোকে আরও দুর্বল করে তুলছে। ফলে তারা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে পারছে না, আস্থা হারাচ্ছে বিনিয়োগকারীরাও।
বাংলাদেশে বিদেশি ব্যাংক বা বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা এখন ব্যাংকিং সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দেখছে। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনো নতুন বিদেশি ব্যাংক এখানে কার্যক্রম শুরু করেনি, বরং কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন: স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড, হংকং ব্যাংক তাদের ঝুঁকির মান পুনর্মূল্যায়ন করেছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনে বাংলাদেশ এখন “উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাংকিং দেশ” হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এটি শুধু ব্যাংক নয়, গোটা অর্থনীতির সুনামের উপরও আঘাত।
জনগণের ব্যাংক এখন কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো একসময় ছিল জনগণের আস্থার প্রতীক। আজ সেগুলো দুর্নীতি, অদক্ষতা ও খেলাপির আস্তানায় পরিণত হয়েছে। যেখানে ব্যাংক কর্মকর্তারা একসময় সৎভাবে কাজ করতেন, এখন তারা ঋণ অনুমোদনে রাজনৈতিক ফোনকলের অপেক্ষা করেন। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ইতিহাসে এক সময় “জনতা ব্যাংক মডেল” উদাহরণ ছিল; আজ সেটিই সবচেয়ে বড় খেলাপির ব্যাংক। ব্যালান্স শিটে এখনো মুনাফার ছবি আঁকা হয়, কিন্তু ক্যাশ রিজার্ভে শূন্যতা, এই হল বাস্তবতা।
ডিজিটাল ব্যাংকিং ও প্রযুক্তি- আশার আলো না মরীচিকা? ডিজিটাল ব্যাংকিং এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু বাস্তবে অনেক ব্যাংক এই সুযোগের সঠিক ব্যবহার করতে পারছে না। ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের নাম করে কিছু প্রতিষ্ঠান কেবল অনলাইন মুখোশ পরেছে। যেখানে বিদেশে ডিজিটাল ব্যাংকগুলো গ্রাহক-সুবিধা ও খরচ কমাতে সফল, আমাদের দেশে সেটি এখনো “PR প্রজেক্ট” মাত্র। কারণ মূল সিস্টেমে দুর্বলতা, সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।
আস্থা পুনরুদ্ধারের পথ কোথায়? ব্যাংক খাতের সংকটের সমাধান এক দিনে সম্ভব নয়। কিন্তু তিনটি মূল পদক্ষেপ জরুরি- স্বচ্ছ ও কঠোর তদারকি: রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ব্যাংক পরিচালনা নিশ্চিত করা। খেলাপি ঋণ আদায়ে আইনগত সংস্কার: ঋণখেলাপিকে বিশেষ সুবিধা না দিয়ে বাস্তব শাস্তির ব্যবস্থা। গ্রাহক আস্থার পুনর্গঠন: নগদ অর্থ প্রবাহে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, ব্যাংকের সেবা মানোন্নয়ন।
বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এখন এক “দুই মুখো” বাস্তবতার মুখোমুখি। ব্যালান্স শিটে হাসি, কিন্তু বাস্তবে কান্না। এই যেন কাগজের সুখের গল্প, বাস্তবের দুঃখের কাব্য। যদি এখনই নীতি ও ব্যবস্থাপনায় সংস্কার না আনা যায়, তবে এই কান্না একদিন ব্যাংকিং ব্যবস্থার মৃত্যু-ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে। এটি দেশের আর্থিক নিরাপত্তার প্রতি সতর্কবার্তা। যদি সমস্যা সমাধানে নীতিনির্ধারক, ব্যাংক ব্যবস্থাপনা এবং বিচারব্যবস্থা সমন্বিতভাবে তৎপর না হয়, তবে ছোটো ত্রুটিও বৃহৎ সংকটে রূপান্তরিত হতে পারে।
অর্থনীতি তখন শুধু সংখ্যার খেলা নয়, হবে আস্থার পতনের ইতিহাস। শেষ কথা “ব্যাংক টেকে আস্থায়, আস্থা টেকে সত্যে, আর সত্য হারালে ব্যাংক বাঁচে না, অর্থনীতিও নয়।”